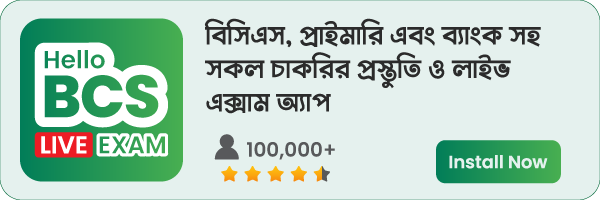বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ২০০ মার্কসের মধ্যে বাংলা অংশ হতে ৩৫ মার্কস এসে থাকে। আবার লিখিত পরীক্ষায় ৯০০ মার্কসের মধ্যে বাংলা ১ম অংশ হতে ১০০ এবং ২য় অংশ হতে ১০০ করে মোট ২০০ মার্কসের প্রশ্ন করা হয়। বাংলা ১ম অর্থাৎ বাংলা সাহিত্য অংশের প্রশ্নে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন আসে।
তাই বাংলা সাহিত্যের পরিপূর্ণ প্রস্তুতির জন্য প্রাচীন যুগ মধ্য যুগের যত খুঁটিনাটি বিষয় রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে ধারণা রাখা প্রয়োজন। আজকের আর্টিকেলে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ ও মধ্যযুগ সম্পর্কে আলোচনা করবো।
বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ (৬৫০-১২০০)
৬৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ বলা হয়।
চর্যাপদ
মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক নিদর্শন ‘চর্যাপদ’ মূলত একটি গানের সংকলন। বৌদ্ধ ধর্মমতের [৪০তম বিসিএস] উল্লেখ থাকা এই গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থও প্রথম কবিতা সংকলন নামেও পরিচিতি লাভ করে। চর্যা শব্দের অর্থ ‘আচরণ’।
পুঁথি আবিষ্কার
→ ১৮৮২ সালে প্রকাশিত ‘Sanskrit Buddhist Literature in Nepal’ গ্রন্থে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সর্বপ্রথম নেপালের বৌদ্ধতান্ত্রিক সাহিত্যের কথা প্রকাশ করেন।
→ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পর তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে নেপালে পুঁথি সংগ্রহের চেষ্টায় যান মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তিনবার তিনি নেপালে যান, ১৮৮৭-৯৮ খ্রিস্টাব্দে ২(দুই) বার এবং শেষবার ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পুঁথি সাহিত্য সংগ্রহের জন্য গিয়েছিলেন তিব্বত ও নেপালে।
চর্যাপদ বাংলার বাইরে পাওয়ার কারণ:
→ বাংলার পাল বংশের রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের। তাদের আমলে চর্যাগীতিকাগুলোর বিকাশ ঘটেছিল। পাল বংশের পরপরই বাংলাদেশে বাংলায় পৌরাণিক হিন্দুধর্ম ও ব্রহ্মাণ্যসংস্কার রাজধর্ম হিসেবে গৃহীত হয়, ফলে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যেরা এ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়। এমনকি সেন রাজাদের প্রতাপের কারণেই বাংলাদেশের বাইরে গিয়ে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয়েছিল।
আরও পড়ুনঃ বিসিএস প্রস্তুতিঃ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে জানা অজানা তথ্য
নামকরণ ও প্রকাশ:
→ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিস্কৃত পুঁথির নাম ‘চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়’।
→ চর্যাপদের প্রাপ্ত পুঁথিতে উল্লেখকৃত সংস্কৃত টীকাকার মুনিদত্তের মতানুসারে এই পদসংগ্রহের নাম- আশ্চর্যচর্যাচয়।
→ ড. প্রবোধ চন্দ্র বাগচী ‘চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়’ নামের পরিকল্পনা করেন।
→ কীর্তিচন্দ্র মুনিদত্তের টীকার তিব্বতি অনুবাদ করেছিলেন “চর্যাগীতিকোষবৃত্তি” নামে।
→ আধুনিক পন্ডিতগণের অনুমান যে পুঁথিটির নাম ছিল চর্যাগীতিকোষ এবং এর সংস্কৃত টীকার নাম ‘চর্য্যাশ্চর্য্যবিনিশ্চয়’।
→ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ধারণা ছিল তিনি চর্যাগীতি সংগ্রহের মূল পুঁথিই (টীকা সহ) আবিস্কার করেছেন। কিন্তু সকল পণ্ডিতই পরবর্তীকালে এ বিষয়ে একমত যে, শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত পুঁথিটি আসলে বৃত্তি বা টীকার।
→ ১৯১৬ খ্রি. (১৩২৩ বাংলা) হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কর্তৃক সম্পাদনায় কলকাতার ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ’ থেকে ‘হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা’ নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।
→ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের (১৮ জুন ১৯২১) প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন।
চর্যাপদের ভাষা বিতর্কনিয়ে আলোচনা :
→ ১৯২০ সালে বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রথম চর্যাপদের ভাষা নিয়ে আলোচনা করেন।
→ চর্যাপদের ভাষায় প্রভাব রয়েছে হিন্দি, অসমিয়া, উড়িয়া, অপভ্রংশ (মৈথিলী) প্রভৃতি ভাষার। তাই অন্যান্য ভাষার ভাষাবিদরাও তাদের ভাষার সাহিত্য বলে দাবী করেন। এ থেকে মুক্তির জন্য ১৯২৬ সালে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ‘Origin and Development of Bengali Literature ’ নামক বিখ্যাত গ্রন্থে এর ভাষাতাত্ত্বিক ক্সবশিষ্ট্য প্রথম আলোচনা করেন। যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন।
→ ১৯২৭ সালে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ চর্যাপদের ধর্মমত সম্পর্কে প্রথম আলোচনা করেন। তাঁর চর্যাপদ সম্পর্কিত গবেষণা গ্রন্থ ‘Buddhist Mystics Songs’ .
→ ১৯৩৮ সালে ড. প্রবোধকুমার বাগচী কর্তৃক চর্যার তিব্বতি অনুবাদ প্রকাশিত হয়।
→ ১৯৪৬ সালে ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত চর্যাগীতির অর্ন্তনিহিত তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন।
চর্যাপদের রচনাকাল :
→ বাংলার পাল বংশের রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। তাদের আমলে চর্যাগীতিকাগুলোর বিকাশ ঘটেছিল। রাহুল সাংকৃত্যায়ন এর মতে, পাল রাজা ধর্মপালের সময়ে লুইপাদ এবং সরহপাদ বর্তমান ছিলেন।
→ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, চর্যার রচনাকাল ৬৫০-১২০০ (সপ্তম হতে দ্বাদশ শতাব্দী) খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।
→ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এর মতে, দশম হতে দ্বাদশ শতাব্দী। (৯৫০-১২০০ খ্রি.)

চর্যাপদের ভাষা :
১৯০৭ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজগ্রন্থাগার থেকে যে পুঁথি সংগ্রহ করেন তা হলো চর্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, সরহপাদের (শরহ বজ্র শাস্ত্রী) দোহাকোষ ও কৃষ্ণাচার্যের (কাহ্নপাদের) দোহাকোষ এবং ডাকার্ণব এই চারটি গ্রন্থের সমন্বয়।
এদের মধ্যে একমাত্র চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ই প্রাচীন বাংলায় লেখা, অন্য তিনটি বাংলায় নয় সংস্কৃত অপভ্রংশ ভাষায় রচিত।
→ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, চর্যার ভাষাকে প্রাচীন বাংলা কিংবা প্রাচীন বঙ্গকামরূপী ভাষা বলাই সঙ্গত।
→ চর্যাপদের ভাষাকে কেউ কেউ সন্ধ্যাভাষা বা সান্ধ্য ভাষা বলেছেন।
→ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এ ভাষা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, ‘আলো আঁধারি ভাষা কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না। যাহারা সাধন ভজন করেন, তাহারাই সে কথা বুঝিবেন, আমাদের বুঝিয়া কাজ নাই।’
এ কারণে চর্যার ভাষা সন্ধ্যাভাষা । ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চর্যাপদের ভাষাকে পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা মনে করেন।
চর্যাপদের ছন্দ : এটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। এর ভাষারীতি কথ্য। এতে সংস্কৃত পজ্ঝটিকা ছন্দের প্রভাব আছে।
চর্যা রচয়িতাগণ :
→ চর্যাপদে মোট ৫০টি পদের ২৩ জন পদকর্তার নাম পাওয়া যায়। আরও একজন পদকর্তার নাম আছে কিন্তু তার পদটি নেই। সেটি ধরলে চর্যার সংখ্যা ৫১টি এবং পদকর্তা ২৪ জন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, চর্যাপদে পদের সংখ্যা ৫০টি। ড. সুকুমার সেনের মতে, চর্যাপদে পদের সংখ্যা ৫১টি।
→ পদকর্তাগণ পদ (কবিতা) রচনা করতেন বলে তাদের সম্মান সূচক পাদনাম বলা হতো।
পাদ >পা। উল্লেখযোগ্য পদকর্তাগণ হলেন- লুইপা, কাহ্নপা, শবরপা (সবর), শান্তিপা, ভুসুকুপা, ঢেগুনপা, ডোম্বীপা, কুক্কুরীপা (মহিলা পদকর্তাহিসেবে বিবেচনা করা হয়), সরহপা, তন্ত্রীপা, মহীধরপা, কঙ্কনপা, লাড়ীডোম্বীপা।
→ ড. হরপ্রসাদশাস্ত্রী ও অধিকাংশের মতে, চর্যাপদের আদি কবি- লুইপা (১, ২৯ নং পদ ২ টি রচনা করেন)। কারণ তিনি প্রথম পদটির রচনা করেছেন।
লুইপা রচিত চর্যাপদের প্রথম পদটি হল- ‘কাআ তরুবর পাঞ্চ বি ডাল/ চঞ্চল চীএ পৈঠা কাল।’
→ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে আদি কবি- শবরপা (২৮, ৫০ নং পদ ২ টি রচনা করেন) (প্রাচীন কবি)
→ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে ‘শবরপা’ বাংলাদেশের লোক ছিলেন।
→ চর্যাপদের পদকর্তা হলেও লাড়ীডোম্বীপার একটি পদের কথা উল্লেখ থাকলেও তার পদটি নেই।
→ শেষপদ রচয়িতা হিসেবে সরহপাদকে বিবেচনা করা হয়।
আরও পড়ুনঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর জীবনী ও সাহিত্য কর্ম
চর্যাপদের পদসংখ্যা :
→ চর্যাপদের প্রাপ্ত পুঁথিতে ৫১ টি পদ ছিল। তার মধ্যে একটি (১১ সংখ্যক) পদ টীকাকার ব্যাখা করেন নি।
→ আবার পুঁথিতে কয়েকটি পাতা নষ্ট হওয়ায় তিনটি সম্পূর্ণ (২৪, ২৫ ও ৪৮ নং) পদ এবং একটি (২৩) পদের শেষাংশ পাওয়া যায় নি। তাই পুঁথিতে সর্বসমেত সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ পাওয়া গেছে।
→ ২৩ নং পদের ৬টি পঙক্তি পাওয়া গেছে , বাকি ৪টি পঙক্তি পাওয়া যায়নি। এর রচয়িতা ভুসুকুপা। তাই অনেকে বলে থাকেন ৪৬.৬০টি পদ পাওয়া যায়।
চর্যার প্রথম পদ রচয়িতা— লুইপা
২৪ নং পদটির রচয়িতা—- কাহ্নপা
২৫ নং পদটির রচয়িতা—- তন্ত্রীপা
৪৮ নং পদটির রচয়িতা—- কুক্কুরীপা (২, ২০, ৪৮)
→ চর্যাপদের কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পদ রচনা করেন কাহ্নপা [৩৫তম বিসিএস]। তিনি মোট ১৩টি পদ রচনা করেন। কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক ১২টি পদ সংগৃহীত হয়।
পদগুলো ৭, ৯, ১০, ১১, ১৩, ১৮, ১৯, ৩৬, ৪০, ৪২, ৪৫, ২৪।
→ ভুসুকুপা-এর পদসংখ্যা ৮টি। সংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় পদকর্তা। ভুসুকুপা নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দেন। তিনি নিজেই বলেছেন- ‘আমি ভুসুকু বাঙালী হলাম বলে’।
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে,চর্যাপদের আধুনিক বা সর্বশেষ পদকর্তা- ‘ভুসুকুপা’।
→ চর্যাপদের পদকর্তার পদের সংখ্যা

মোট পদের সংখ্যা ৫০টি। যথাঃ
কাহ্নপা — ১৩টি আর্যদেব,
ভুসুকুপা — ৮টি
সরহপা — ৪টি
কুক্করীপা — ৩টি
লুইপা— ২টি
শবরপা— ২টি
শান্তিপা — ২টি
কঙ্কনপা, কম্বলাম্বর, গুন্ডরিপা, চাটিলপা, জয়নন্দী, ডোম্বীপা, ঢেন্ডণপা, তন্ত্রীপা, তারকপা, দাড়িকপা, ধামপা, বিরুবাপা, বীণাপা, ভদ্রপা, মহীধরপা — ১টি।
চর্যাপদে মোট ৬টি প্রবাদ বাক্য পাওয়া যায়। প্রবাদসমূহেরপদকর্তার নামসহ বর্ণিত হলঃ
পদ নং ৬
ভুসুকুপা = আপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী (হরিণের মাংসই তার শত্রু)
পদ নং ৩২
শরহপা = হাতের কাঙ্কন মা লোউ দাপন (হাতের কাঁকন দেখার জন্য দর্পণ প্রয়োজন হয় না)
পদ নং ৩৩
ঢেণ্ডণপা = হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী (হাড়িতে ভাত নেই, অথচ প্রতিদিন প্রেমিকরা এসে ভীড় করে।) ; দুহিল দুধ কি বেণ্টে সামায় (দোহন করা দুধ কি বাটে প্রবেশ করানো যায়?)
পদ নং ৩৯
শরহপা = হাতের কাঙ্কন মা লোউ দাপন (হাতের কাঁকন দেখার জন্য দর্পণ প্রয়োজন হয় না)
পদ নং ৪৪
কঙ্কণপা = আন চাহন্তে আন বিনধা (অন্য চাহিতে অন্য বিনষ্ট)
→ ‘টালত মোর ঘর নাহি পরবেশী’, ‘হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী’ এই পঙ্ক্তি দুটি দ্বারা দারিদ্র্যক্লিষ্ঠ জীবনের চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে।
বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ (১২০০-১৮০০)
১২০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে বাংলা সাহিত্যের মধ্য যুগ বলা হয়।
বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের শুরু ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির আগমনের মাধ্যমে এবং ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের মাধ্যমে শেষ হলেও এর ব্যাপ্তি ধরা হয় ১২০১ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত। মধ্যযুগের এই সময়টা মুসলিম শাসকদের শাসনের আওতায় হওয়ায় বিভিন্ন শাসকবর্গের ভূমিকা আলোচিত এবং সমালোচিত।
বাংলায় মুসলিম শাসন ও সাহিত্যে তাদের ভূমিকা বিবেচনা করতে গেলে মধ্যযুগকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–
তুর্কি যুগ (১২০১-১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ)ঃ তুর্কি শাসকদের সময়ে বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ পরিলক্ষিত হয়।
সুলতানি যুগ (১৩৫১-১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দ)ঃ বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় পাঠান সুলতানদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ড. দীনেশচন্দ্র সেন এই সময়কে ‘গৌড়ীয় যুগ’ বলেও অভিহিত করেছেন। কারণ গৌড়কে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিখ্যাত নাম ‘আলাউদ্দিন হুসেন শাহ। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় বিপ্রদাস পিপিলাই ‘মনসাবিজয়’ এবং ক্সজনুদ্দীন ‘রসুলবিজয়’ কাব্য রচনা করেন।
মুঘল শাসনামল (১৫৭৬-১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ)ঃ জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবর ভারতের মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের নাম তু্যুক-ই-বাবরি। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের নাম তু্যুক-ই-জাহাঙ্গীর।
বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ
মধ্যযুগের ১২০১-১৩৫০ সাল পর্যন্ত সময়কে ভাষাবিজ্ঞানীরা ‘অন্ধকার যুগ’ বা ‘বন্ধ্যা যুগ’ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ড. হুমায়ুন আজাদ তাঁর ‘লাল নীল দীপাবলী’ গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ১৭) লিখেছেন- ‘১২০০ থেকে ১৩৫০ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রচিত কোন সাহিত্য কর্মের পরিচয় পাওয়া যায় না বলে তুর্কি শাসকদের এ-সময়টাকে বলা হয় ‘অন্ধকার যুগ’। পন্ডিতেরা এ সময়টাকে নিয়ে অনেক ভেবেছেন, অনেক আলোচনা করেছেন, কিন্তু কেউ অন্ধকার সরিয়ে ফেলতে পারেন নি।

সময়টির দিকে তাকালে তাই চোখে কোন আলো আসে না, কেবল আঁধার ঢাকা চারদিক।’
কিন্তু, ওয়াকিল আহমেদ তাঁর ‘বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত’ (পৃষ্ঠা- ১০৫) গ্রন্থে লিখেছেন- ‘বাংলা সাহিত্যের কথিত ‘অন্ধকার যুগ’ মোটেই সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্বের যুগ ছিল না। ধর্ম- শিক্ষা, শিল্প চর্চার দায়িত্ব যাদের উপর ন্যস্ত ছিল, তারা সীমিত আকারে হলেও শিক্ষা সাহিত্য চর্চায় নিয়োজিত ছিলেন। তবে কি হিন্দু কি মুসলমান কেউ লোকভাষা বাংলাকে গ্রহণ করেন নি। বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন না থাকার এটাই মুখ্য কারণ।’
আরও পড়ুনঃ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে নানা জানা অজানা তথ্য জেনে নিন
কারণ :
→ ১২০১ মতান্তরে ১২০৪ সালে তুর্কী জাতির অধিনায়ক ইসলাম ধর্মাবলম্বী ইখতিয়ার উদ্দিন বিন বখতিয়ার খলজী হিন্দু শাসক লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমান শাসনের সূত্রপাতে দেশে রাজনৈতিক অরাজকতার অনুমান করে কোন কোন পণ্ডিত এ সময়কে বাংলা সাহিত্যের ‘অন্ধকার যুগ’ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ দেড়শ বছরে বাংলা সাহিত্যের কোন নিদর্শন না পাওয়া গেলেও সংস্কৃত সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়।
এতে অনেকের মতবিরোধ দেখা যায়। কারণ, এ সময়ে বাংলা সাহিত্যের ব্যাপক নিদর্শন পাওয়া না গেলেও অন্যান্য ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির নিদর্শন থাকাতে অন্ধকার যুগের অপবাদের অসারতা প্রমাণিত হয়।
→ এ সময়ের প্রথমেই প্রাকৃত পিঙ্গলের মত প্রাকৃত ভাষার গীতিকবিতা গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে। রামাই পণ্ডিত রচিত শূন্যপুরাণ, ডাক ও খনার বচন, হলায়ূধ মিশ্র রচিত সেক শুভোদয়া-এর অন্তর্গত পীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক প্রভৃতি এ সময়ের বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির নতুন হিসেবে উল্লেখযোগ্য।
শূন্যপূরাণ
রামাই পণ্ডিত রচিত ধর্মপূজার শাস্ত্রগ্রন্থ। ধর্মীয় তত্ত্বের গ্রন্থ – গদ্যপদ্য মিশ্রিত চম্পুকাব্য। এ গ্রন্থের অন্তর্গত ‘নিরঞ্জনের উষ্মা’ বা ‘নিরঞ্জনের রুষ্মা’ কবিতাটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, তা তুর্কি
মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের পরের, অন্তত ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকের রচনা। এতে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের কথা আলোচিত হয়েছে।
সেক শুভোদয়া
রাজা লক্ষণ সেনের সভাকবি হলায়ূধ মিশ্ররচিত সেক শুভোদয়া সংস্কৃত গদ্যেপদ্যে লেখা চষ্পুকাব্য। গ্রন্থটি রাজা লক্ষ্মণ সেন ও শেখ জালালুদ্দীন তাবরেজির অলৌকিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত।
সেক শুভোদয়া অর্থাৎ শেখের গে․রব ব্যাখ্যাই এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য।
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য
মধ্যযুগের প্রথম নিদর্শন অথবা প্রথম কাব্য বড়– চণ্ডীদাসের (মধ্যযুগের প্রথম কবি) সর্বজন স্বীকৃত ও খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ (চৌদ্দ শতক-পনের শতক) কাব্য। এটি বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় কাব্য। মধ্যযুগের এ শ্রেষ্ঠ নিদর্শনটির সম্পর্কে নিচে বর্ণনা করা হল–
→ একক কবির রচনা হিসেবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য বাংলা সাহিত্যের প্রথম কাব্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য একজন রচনা করেছেন কিন্তু চর্যাপদ চব্বিশজন রচনা করেছেন।
পুঁথি আবিস্কার :
১৯০৯ খ্রি. (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) বসন্তরঞ্জন রায় (উপাধি: বিদ্বদ্বল্লভ) পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রামে এক গৃহস্থ বাড়ির গোয়াল ঘরের টিনের চালার নিচ থেকে অযত্নে রক্ষিত এ কাব্য আবিস্কার করেন। বর্তমানে এই পুঁথিটি ২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্ল রায় রোডস্থ ‘বঙ্গীয়
সাহিত্য পরিষদের’ পুঁথিশালায় রক্ষিত আছে।
→ বৈষ্ণব মহান্ত শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র- বংশজাত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এর অধিকারে এ গ্রন্থটি রক্ষিত ছিল।
→ পুঁথিটির প্রথমদিকের দুটি পাতা এবং শেষের পাতাটি ছিল না। পুঁথির ৪৫২ পৃষ্ঠার মাঝের ৪৫ পৃষ্ঠাও পাওয়া যায় নি।
সাধারণ রীতি অনুযায়ী পুঁথির প্রথম দিকে দেবতার প্রশংসা, কবির পরিচয় ও গ্রন্থনাম উল্লেখিত হয় এবং শেষ দিকের পাতায় পুঁথির রচনাকাল ও লিপিকাল লিখিত থাকে। প্রথম ও শেষ অংশ খণ্ডিত থাকায় কবির আত্মপরিচয় ও রচনাকাল লোকচক্ষুর আড়ালেই থেকে যায়।
→ ১৯১৬ সালে (১৩২৩ বাংলা) বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় কলকাতা ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ’ থেকে প্রকাশিত হয়।
→ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কবির পরিচয় : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য রচনা করেন বড়–চণ্ডীদাস। ইহা তার উপাধি। তার প্রকৃত নাম অনন্ত বড়–য়া বা অনন্ত বড়াই।
→ কবির কাল: সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায়ের সংগৃহীত তথ্যমতে, ১৩৮৬ থেকে ১৪০০ খ্রি. কোন এক সময়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, ১৩৭০-১৪৩৩ খ্রি।
→ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপি ১৪৩৬-১৫২০ খ্রি. অপেক্ষা প্রাচীন এবং তা ১৩৪০-১৪৪০ খ্রি. মধ্যে রচিত।
→ পুঁথির নামকরণ: পুঁথিতে প্রাপ্ত একটি চিরকুট অনুসারে এই কাব্যের প্রকৃত নাম ‘শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ’।
→ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য মোট ১৩ (তের) খণ্ডে বিভক্ত- জন্ম খণ্ড, তাম্বুল খণ্ড, দান খণ্ড, নে․কা খণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্র খণ্ড, বৃন্দাবন খণ্ড, কালিয়দমন খণ্ড, যমুনা খণ্ড,হরখণ্ড, বানখণ্ড,বংশীখণ্ড, ও রাধা বিরহ।
→ ড. আহমদ শরীফ এই কাব্যকে শ্রীকৃষ্ণ ধামালি নামে অভিহিত করেন।
→ গঠনরীতিতে ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্য মূলত- ‘নাটগীতি’। [৩৮তম বিসিএস]
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের নামকরণ
পুঁথিতে প্রাপ্ত একটি চিরকুট অনুসারে এই কাব্যের প্রকৃত নাম হল “শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ”। কিন্তু সম্পাদক কাব্যে কৃষ্ণলীলা সম্পর্কিত বিষয়বস্তুদেখে নামকরণ করেন “শ্রীকৃষ্ণকীর্তন”। তাঁর বক্তব্য ছিল, “পুঁথির আদ্যন্তহীন খণ্ডিতাংশে কবির দেশকালাদির কথা দূরে থাকুক, পুঁথির নাম পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।”

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের চরিত্র পরিচিতি
→ প্রধান চরিত্র : রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই। এই তিন চরিত্রের মধ্যে রাধাকে কেন্দ্র করেই কাব্যের আখ্যান বস্তুর বিকাশ ঘটেছে।
→ রাধা : পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে রাধা হলো মানবাত্মার প্রতীক যে পরমাত্মাকে পাবার জন্য সারাক্ষণ ব্যাকুল। কিন্তু বড়–চণ্ডীদাস এর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে রাধা চরিত্র অপরূপ সুন্দরী এক নারী গোয়ালার ঘরে যার জন্ম। বাল্যকালে নপুংসক অপর এক গোয়ালা আয়েন ঘোষের সহীত তার বিয়ে হয়। রাধার দায়িত্বভার অর্পণ করা হয় আয়েন ঘোষের পিসিমার উপর। তিনিই রাধা কৃষ্ণের সম্পর্ক সৃষ্টিতে সহযোগিতা করেন।
→ কৃষ্ণ : পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে কৃষ্ণ হলো পরমাত্মা বা স্রষ্টা। কিন্তু বড়–চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে কৃষ্ণ হলেন সুদর্শন এক রাখাল যুবক।
→ বড়াই : বড়াই হলেন রাধা কৃষ্ণ প্রেমলীলার দূত। [২৮তম বিসিএস]
চণ্ডীদাসের সমস্যা
চণ্ডীদাসের পদাবলী দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত থাকলেও একাধিক চণ্ডীদাস সম্পর্কিত চণ্ডীদাস সমস্যার উদ্ভব হয়েছে ১৯১৬ খ্রি. (১৩২৩ বাংলা সন) বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রকাশের পর থেকে।
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তিনজন চণ্ডীদাসের কথা উল্লেখ করেছেন– বড়–চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস ও দ্বীন চণ্ডীদাস। এদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বড়–চণ্ডীদাস
সবচেয়ে প্রাচীন। তবে সকল পণ্ডিতগণের মতামত অনুসারে চারজন চণ্ডীদাস সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।
বাংলা সাহিত্যের বিষয়ভিত্তিক এই আর্টিকেলের বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের যত ধরণের খুঁটিনাটি বিষয়বস্তু রয়েছে সেইগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আশা করি প্রাচীন ও মধ্য যুগের সমস্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে আপনাদের কিছুটা হলেও ধারণা হবে।
হেলো বিসিএস এর সাথে থাকুন। ধন্যবাদ।