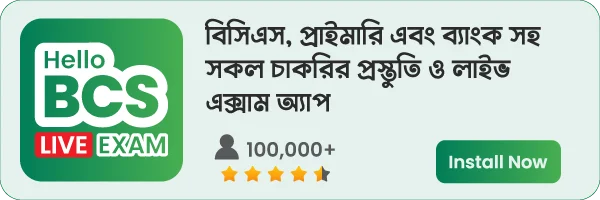বাংলা প্রথম পত্র হতে দ্বিতীয় পত্র অর্থাৎ ব্যাকরণের অংশ অনেকে কঠিন মনে করে থাকে। কারণ ব্যাকরণকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথাঃ- ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব, অর্থতত্ত্ব। বাক্য, সমাস, সন্ধি, শব্দ, ধ্বনি, বর্ণ, পদাশ্রিত নিদর্শন, বচন, উপসর্গ,অনুসর্গ,বানান, সমার্থক শব্দ,এক কথায় প্রকাশ, পরিভাষা, বাগধারা, প্রবাদ প্রবচন, অনুবাদ রচনা ইত্যাদি সব বিষয়গুলো এই চারটি ভাগের মধ্যে বিভক্ত। এই সবগুলো অংশ থেকে বিসিএস, ব্যাংক, প্রাইমারি সহ প্রায় সব চাকরি পরীক্ষায় প্রশ্ন হয়ে থাকে। আজকের আর্টিকেলে বাংলা ব্যাকরণের বাক্য সম্পর্কে আলোচনা করবো।
বাক্য কাকে বলে?
বাক্য শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কথ্য বা কথিত বিষয়। যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি বক্তার কোন মনোভাবকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে তাকে বাক্য বলে।
- বাক্যের মৌলিক উপাদান শব্দ।
- ভাষার মূল উপকরণ বাক্য।
বাক্যের গুণ
ভাষার বিচারে বাক্যের তিনটা গুণ থাকা আবশ্যক। যথাঃ
১) আকাঙ্ক্ষা
২) আসত্তি
৩) যোগ্যতা
১) আকাঙ্ক্ষা
বাক্যের অর্থ পরিষ্কার ভাবে বোঝার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা তা-ই আকাঙ্ক্ষা ।
উদাহরণঃ মা আমাকে অনেক আদর …
উপরের বাক্যে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ করছে না। বাক্য শেষ হওয়ার পরও আরো কিছু শোনার আকাঙ্ক্ষা থেকে যাচ্ছে। সুতরাং, বাক্যের আকাঙ্ক্ষা গুণটি নেই। তাই এটি বাক্য নয়।
সম্পূর্ণ বাক্যটি হবে মা আমাকে অনেক আদর করে।
এটি শোনার পর আর কিছু শোনার আগ্রহ বাকি থাকছে না। সুতরাং এটি আকাঙ্ক্ষা গুণ সম্পন্ন একটি সার্থক বাক্য।
২) আসত্তিঃ
বাক্যে অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসই আসত্তি।
উদাহরণঃ আছে কলম আমার একটি। বাক্যের পদগুলো সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো হয়নি। এই পদগুলো সুশৃঙ্খলভাবে সাজালে বাক্যটি হবে— আমার একটি কলম আছে। যা একটি ভাবকে প্রকাশ করছে।
৩)যোগ্যতাঃ
বাক্যস্থিত পদসমূহের অর্থগত এবং ভাবগত মিলবন্ধনের নাম যোগ্যতা।
উদাহরণঃমাছ আকাশে উড়ে। কিন্তু মাছের আকাশে উড়ার যোগ্যতা নেই। সুতরাং বাক্যটি যোগ্যতাহীন। অতএব বাক্যটি হবে পাখি আকাশে উড়ে।
যোগ্যতার সাথে জড়িত বিষয়গুলো হচ্ছে –
১. উপমার ভুল প্রয়োগ
২. দুর্বোধ্যতা
৩. রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা
৪. বাহুল্য-দোষ
৫. গুরুচণ্ডালী দোষ
৬. বাগধারার শব্দ পরিবর্তন

আরও পড়ুনঃ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম
১. উপমার ভুল প্রয়োগঃ উপমা- অলংকার সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। এগুলোর প্রয়োগে কোন ভুল হলে বাক্য তার ভাবগত যোগ্যতা হারাবে।
যেমনঃ আমার হৃদয়- মন্দিরে আশার বীজ উপ্ত হল।
বাক্যটিতে উপমার ভুল প্রয়োগ হয়েছে। কারণ, বীজ মন্দিরে উপ্ত হয় না/ বপন করা হয় না। বীজ বপন করা হয় ক্ষেতে।
সুতরাং বলতে হবে আমার হৃদয়- ক্ষেত্রে আশার বীজ উপ্ত হল।
২. দুর্বোধ্যতাঃ অপ্রচলিত কিংবা দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে বাক্য তার যোগ্যতা গুণ হারায়। এই ধরনের শব্দ বাক্যের শব্দগুলোর মধ্যে অর্থগত মিলবন্ধন নষ্ট করে।
যেমন- এ কী প্রপঞ্চ!
বাক্যটির প্রপঞ্চ শব্দটি অপ্রচলিত, একই সঙ্গে দুর্বোধ্য। তাই বাক্যটির অর্থ পরিস্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে না। ফলে বাক্যের পদগুলোর মধ্যের অর্থগত মিলবন্ধন বিনষ্ট হয়েছে। তাই এটি কোন যোগ্যতা সম্পন্ন সার্থক বাক্য হতে পারেনি।
৩. রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা : বাক্যে শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে, শব্দগুলো যাতে তাদের রীতিসিদ্ধ অর্থ অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়। শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক বা রীতিসিদ্ধ অর্থ ভিন্ন হলে, অবশ্যই রীতিসিদ্ধ অর্থে শব্দ ব্যবহার করতে হবে। নয়তো শব্দটির সঙ্গে বাক্যের অন্য শব্দগুলোর অর্থগত মিলবন্ধন নষ্ট হবে।
যেমনঃ ‘বাধিত ’ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ‘ বাধাপ্রাপ্ত”। আর ব্যবহারিক বা রীতিসিদ্ধ অর্থ হলো ‘ কৃতজ্ঞ ’। শব্দটি ব্যবহারের সময় কৃতজ্ঞ অর্থেই ব্যবহার করতে হবে। নয়তো তা অর্থ বিকৃত করবে। ফলে বাক্যটি যোগ্যতা গুণ হারাবে।
৪. বাহুল্য-দোষঃ প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ বা শব্দাংশ ব্যবহার করলে শব্দের অর্থগত যোগ্যতা নষ্ট হয়। ফলে বাক্যও যোগ্যতা গুণ হারায়। শব্দকে বহুবচন করার সময় একাধিক বহুবচনবোধক শব্দ বা শব্দাংশ ব্যবহার করা একটি সাধারণ বাহুল্য দোষ।
যেমন- ‘ সব মানুষেরা ’ বাহুল্য দোষে দুষ্ট শব্দ। যোগ্যতা গুণ সম্পন্ন বাক্যে ‘সব মানুষ ’ বা ‘ মানুষেরা’- এই দুটির যে কোন একটি ব্যবহার করতে হবে।
৫. গুরুচণ্ডালী দোষঃ বাক্যে তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ ও তদ্ভব বা খাঁটি বাংলা শব্দ একসঙ্গে ব্যবহার করলে তাকে গুরুচণ্ডালী দোষ বলে। সেটি বাক্যের যোগ্যতা গুণ নষ্ট করে। কারণ, তাতে পদগুলোর ভাবগত মিল নষ্ট হয়।
যেমন- ‘ গরুর গাড়ি ’ শব্দদুটো সংশিলষ্ট শব্দ এবং দুটিই খাঁটি বাংলা শব্দ। আমরা যদি একে ‘ গরুর শকট ’ বলি, তা শুনতে যেমন বিশ্রী শোনায়, তেমনি শব্দদুটোর ভাবগত মিলও আর থাকে না। এটিই গুরুচণ্ডালী দোষ।
এরকম‘ শবদাহ’কে ‘ মড়াদাহ ’ কিংবা ‘ শবপোড়া ’, ‘ মড়াপোড়া’কে ‘ শবপোড়া ’ বা ‘ মড়াদাহ ’ বললে তা গুরুচণ্ডালী দোষ হবে।
৬. বাগধারার শব্দ পরিবর্তনঃ বাগধারা ভাষার একটি ঐতিহ্য। বাগধারা ব্যবহার করার সময় এগুলোর কোন পরিবর্তন করলে বাগধারার ভাবগত যোগ্যতা নষ্ট হয়। ফলে বাক্য তার যোগ্যতা গুণ হারায়।
যেমন- যদি বলা হয়, “ অরণ্যে ক্রন্দন ’ তাহলে গুরুচণ্ডালী দোষও হয় না। কিন্তু বাগধারাটির শব্দ পরিবর্তন করার কারণে এটি তার ভাবগত যোগ্যতা হারিয়েছে। যোগ্যতা সম্পন্ন বাক্য গঠন করতে হলে প্রচলিত বাগধারাটিই লিখতে হবে। অর্থাৎ ‘ অরণ্যে রোদন’ই লিখতে হবে।
বাক্যের প্রকারভেদঃ
গঠনগত ভাবে বাক্য ৩ প্রকার। যথাঃ
১) সরল বাক্য
২) জটিল বাক্য
৩) যৌগিক বাক্য
১) সরল বাক্য
যে বাক্যে একটিমাত্র কর্তা (উদ্দেশ্য) এবং একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়) থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যথা- পুকুরে পদ্মফু জন্মে। এখানে ‘পদ্মফুল’ উদ্দেশ ̈ এবং ‘জন্মে’ বিধেয়। এ রকম কিছু উদাহরণ :
- বৃষ্টি হচ্ছে।
- তোমরা বাড়ি যাও।
- ধনীরা প্রায়ই কৃপণ হয়।
- মিথ্যাবাদীকে কেউ ভালবাসে না।
- শিক্ষিত লোকেরা অত ̈ন্ত বুদ্ধিমান।
- ধনীরা প্রায়ই কৃপণ হয়।
- মা শিশুকে ভালোবাসে।
- হযরত মোহাম্মদ (স.) ছিলেন একজন আদর্শ মানব। স]
- সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।
সরল বাক্য চেনার সহজ উপায়
- সরল বাক্যে একটিই সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। একটি সরল বাক্যে একটি বা একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া থাকতে পারে। যেমন- কেহ কহিয়া না দিলেও (অসমাপিকা ক্রিয়া) তপোবন বলিয়া বোধ হইতেছে (সমাপিকা ক্রিয়া)।
- সরল বাক্যে ক্রিয়াপদ উহ্য থাকতে পারে। যেমন- জ্ঞানী লোক সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।
- সরল বাক্যের ভেতরে কোন খণ্ডবাক্য বা একাধিক পূর্ণবাক্য থাকে না। যেমন- চেহারা নিষ্প্রভ হলেও তার মুখাবয়বে একটা পরিতৃপ্তির আভা ছিল।
২) জটিল বাক্য
যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্য ও তাকে আশ্রয় বা অবলম্বন করে একাধিক খণ্ডবাক্য থাকে,
তাকে জটিল বা মিশ্র বাক্য বলে। যেমনঃ
- যে পরিশ্রম করে, সে-ই সুখ লাভ করে। (প্রথম অংশটি আশ্রিত খণ্ডবাক্য, দ্বিতীয়টি প্রধান খণ্ডবাক্য)
- যত পড়বে,/ তত শিখবে,/ তত ভুলবে। (প্রথম দুটি অংশ আশ্রিত খণ্ডবাক্য শেষ অংশটি প্রধান খণ্ডবাক্য)
- সে যে অপরাধ করেছে তা মুখ দেখেই বুঝেছি
- যিনি পরের উপকার করেন তাঁকে সবাই শ্রদ্ধা করে
জটিল বা মিশ্র বাক্য চেনার সহজ উপায়
- জটিল বা মিশ্র বাকে একাধিক খণ্ডবাক্য থাকে। এদের মধ্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্য এবং অন্যগুলো সেই বাক্যের উপর নির্ভর করে। যেমনঃ যেহেতু তুমি বেশি নম্বর পেয়েছ, সুতরাং তুমি প্রথম হবে।
- অধিকাংশ জটিল বাক্যে প্রতিটি খণ্ডবাক্য এর পর কমা (,) থাকে। যথা- যিনি পরের উপকার করেন, তাঁকে সবাই শ্রদ্ধা করে।
- জটিল বাক্যের সাপেক্ষ সর্বনাম ও নিত্য সম্বন্ধীয় যোজক যোগ করতে হয়। যথা-
সাপেক্ষ সর্বনাম : যে….সে, যা….তা, যিনি….তিনি, যারা…. তারা। যেমনঃ যিনি বিদ্বান, তিনি সর্বত্র আদরণীয়।
নিত্য সম্বন্ধীয় যোজক: যখন…. তখন, যেমন…. তেমন, বরং…. তবু, যেইনা….অমনি, যেহেতু….সেহেতু/সেজন ̈। যেমনঃযখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে।
৩) যৌগিক বাক্য
একাধিক সরল বাক্য কোন অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত হয়ে একটি বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমনঃ
- তার বয়স হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি হয়নি। (সরল বাক্য দুটি- তার বয়স হয়েছে, তার বুদ্ধি হয়নি)
- সে খুব শক্তিশালী এবং বুদ্ধিমান। (সরল বাক্য দুটি- সে খুব শক্তিশালী, সে খুব বুদ্ধিমান)
- ধনীদের ধন আছে, কিন্তু তারা প্রায়ই কৃপণ হয়।
- বুঝে শুনে উত্তর দাও নতুবা ভুল হবে।
- এতক্ষণ অপেক্ষা করলাম কিন্তু গাড়ি পেলাম না।
- সে আসতে চায়, তথাপি আসতে পারে না।
- তাঁর বুদ্ধি হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি পাকেনি।
- সত্য কথা বলিনি, তাই বিপদে পড়েছি।
যৌগিক বাক্য চেনার সহজ উপায়
যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত নিরপেক্ষ বাক্যগুলো আর, এবং, ও, বা, কিন্তু, অথবা, অথচ, কিংবা, বরং, তথাপি, তবে, তবে কি না, নতুবা, তবু, হয়..নয়, হয়.. না হয়, কেন..না, তত্রাচ, অপিচ প্রভৃতি অব্যয় যোগে সংযুক্ত বা সমন্বিত থাকে। তবে কোন অব্যয় ছাড়াও দুটি সরল বাক্য
একসঙ্গে হয়ে যৌগিক বাক্য গঠন করতে পারে।

আরও পড়ুনঃ বিসিএস প্রস্তুতি:বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বাক্য রূপান্তর
বাক্যের অর্থ পরিবর্তন না করে বাক্যের প্রকাশভঙ্গি বা গঠনরীতিতে পরিবর্তন করাকেই বাক্য রূপান্তর বলা হয়।
- সরল থেকে জটিল বাক্যে রূপান্তর:
সরল বাক্যের কোন একটি অংশকে সম্প্রসারিত করে একটি খন্ডবাক্যে রূপান্তরিত
করতে হয় এবং তার খণ্ডবাক্যটির সঙ্গে মূল বাক্যের সংযোগ করতে উপরোক্ত সাপেক্ষ সর্বনাম বা সাপেক্ষ অব্যয়গুলোর কোনটি ব্যবহার করতে হয়। যেমনঃ
সরল বাক্য: ভাল ছেলেরা কম্পিউটারে বসেও ইন্টারনেটে পড়াশুনা করে।
জটিল বাক্য: যারা ভাল ছেলে, তারা কম্পিউটারে বসেও ইন্টারনেটে পড়াশুনা করে।
সরল বাক্য: ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও।
জটিল বাক্য: যে ভিক্ষা চায়, তাকে ভিক্ষা দাও।
সরল বাক্য: পড়া শোনা করলে চিন্তা কী?
জটিল বাক্য: যে পড়া শোনা করে, তার চিন্তা কী?
সরল বাক্য: অন্ধকে আলো দাও।
জটিল বাক্য যে অন্ধ, তাকে আলো দাও।
সরল বাক্য তোমার কথা আজীবন মনে থাকবে।
জটিল বাক্য যতদিন জীবিত থাকব, ততদিন তোমার কথা মনে থাকবে।
- জটিল থেকে সরল বাক্যে রূপান্তর:
জটিল বাক্যটির অপ্রধান/ আশ্রিত খণ্ডবাক্যটিকে একটি শব্দ বা শব্দাংশে পরিণত
করে সরল বাক্যে রূপান্তর করতে হয়। যেমন:
জটিল বাক্য: যত দিন বেঁচে থাকব, এ কথা মনে রাখব।
- সরল বাক্য: আজীবন এ কথা মনে রাখব।
জটিল বাক্য: যদি দোষ স্বীকার কর তাহলে তোমাকে কোন শাস্তি দেব না।
- দোষ স্বীকার করলে তোমাকে কোন শাস্তি দেব না।
যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই এ কথা বিশ্বাস করবে।
- সরল বাক্য: বুদ্ধিহীনরাই এ কথা বিশ্বাস করবে।
জটিল বাক্য: যদি কথা রাখেন, তাহলে আপনাকে বলতে পারি।
- সরল বাক্য: কথা রাখলে আপনাকে বলতে পারি।
সরল থেকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর:
সরল বাক্যের কোন অংশকে সম্প্রসারিত করে একটি পূর্ণ বাক্যে রূপান্তরিত করতে হয় এবং পূর্ণ বাক্যটির সঙ্গে মূল বাক্যের সংযোগ করতে উপরোক্ত অব্যয়গুলো ব্যবহার করতে হবে। যেমনঃ
- সরল বাক্য: দোষ স্বীকার করলে তোমাকে কোন শাস্তি দেব না
যৌগিক বাক্য: দোষ স্বীকার কর, তাহলে তোমাকে কোন শাস্তি দেব না। (এক্ষেত্রে ‘তাহলে’ অব্যয়টি ব্যবহার না করলেও চলতো)
সরল বাক্য: আমি বহু কষ্টে শিক্ষা লাভ করেছি।
যৌগিক বাক্য: আমি বহু কষ্ট করেছি এবং/ ফলে শিক্ষা লাভ করেছি।
সরল বাক্য: পরিশ্রম করলে ফল পাবে।
যৌগিক বাক্য: পরিশ্রম করবে এবং ফল পাবে।

সরল বাক্য: মিথ্যা কথা বলে বিপদে পড়েছ।
যৌগিক বাক্য: মিথ্যা কথা বলেছ, তাই বিপদে পড়েছ।
- যৌগক থেকে সরল বাক্যে রূপান্তর:
যৌগিক বাক্যে একাধিক সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। অন্যদিকে সরল বাক্যে একটিই
সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। তাই যৌগিক বাক্যের একটি সমাপিকা ক্রিয়াকে অপরিবর্তিত রেখে বাকিগুলোকে সমাপিকা ক্রিয়ায় পরিণত করতে হবে। যৌগিক বাক্যে একাধিক পূর্ণ বাক্য থাকে এবং তাদের সংযোগ করার জন্য একটি অব্যয় পদ থাকে। সেই অব্যয়টি বাদ দিতে হবে। যেমনঃ
যৌগিক বাক্য: তার বয়স হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি হয়নি। (সমাপিকা ক্রিয়া হয়েছে, হয়নি)
সরল বাক্য: তার বয়স হলেও বুদ্ধি হয়নি। (‘ হয়েছে ’ সমাপিকা ক্রিয়াকে ‘ হলেও অসমাপিকা ক্রিয়ায় রূপান্তরিত করা
হয়েছে)
যৌগিক বাক্য: মেঘ গর্জন করে, তবে ময়ূর নৃত্য করে। (সমাপিকা ক্রিয়া-করে ও করে)
সরল বাক্য: মেঘ গর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে। (‘ করে ’ সমাপিকা ক্রিয়াকে ‘ করলে ’ অসমাপিকা ক্রিয়ায় রূপান্তরিত করা
হয়েছে)
যৌগিক বাক্য: সত্য কথা বলি নি, তাই বিপদে পড়েছি।
সরল বাক্য: সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি।
যৌগিক বাক্য: তিনি ধনী ছিলেন কিন্তু সুখী ছিলেন না।
সরল বাক্য: তিনি ধনী হলেও সুখী ছিলেন না।
- জটিল থেকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর:
জটিল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর করতে হলে এই খণ্ডবাক্যগুলোর পরস্পর নির্ভরতা মুছে দিয়ে স্বাধীন করে দিতে হবে। এজন্য সাপেক্ষ সর্বনাম বা অব্যয়গুলো তুলে দিয়ে যৌগিক বাক্যে ব্যবহৃত অব্যয়গুলোর মধ্যে উপযুক্ত অব্যয়টি বসাতে হবে। পাশাপাশি ক্রিয়াপদের গঠনের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। যেমন
জটিল বাক্য: যদি সে কাল আসে, তাহলে আমি যাব।
যৌগিক বাক্য: সে কাল আসবে এবং আমি যাব।
জটিল বাক্য: যদিও তাঁর টাকা আছে, তবুও তিনি দান করেন না।
যৌগিক বাক্য: তাঁর টাকা আছে, কিন্তু তিনি দান করেন না
জটিল বাক্য: যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে।
যৌগিক বাক্য: বিপদ এবং দুঃখ এক সময়ে আসে।
জটিল বাক্য: সে যেমন কৃপণ তেমন চালাক।
যৌগিক বাক্য: সে কৃপণ ও চালাক।
- যৌগিক থেকে জটিল বাক্যে রূপান্তর: যৌগিক বাক্যে দুইটি পূর্ণ বাক্য কোন অব্যয়ের দ্বারা যুক্ত থাকে। এই অব্যয়টি তুলে দিয়ে সাপেক্ষ সর্বনাম বা অব্যয়ের প্রথমটি প্রথম বাক্যের পূর্বে ও দ্বিতীয়টি দ্বিতীয় বাক্যের পূর্বে বসালেই জটিল বাক্যে রূপান্তরিত হবে। যেমনঃ
যৌগিক বাক্য: দোষ স্বীকার কর, তোমাকে কোন শাস্তি দেব না।
জটিল বাক্য: যদি দোষ স্বীকার কর, তাহলে তোমাকে কোন শাস্তি দেব না।
যৌগিক বাক্য: তিনি অত্যন্ত দরিদ্র কিন্তু তার হৃদয় অত্যন্ত মহৎ।
জটিল বাক্য: যদিও তিনি অত্যন্ত দরিদ্র, তবুও তার হৃদয় অত্যন্ত মহৎ।
যৌগিক বাক্য: এ গ্রামে একটি দরগাহ আছে, সেটি পাঠানযুগে নির্মিত।
জটিল বাক্য: এ গ্রামে যে দরগাহটি আছে, সেটি পাঠানযুগে নির্মিত।
যৌগিক বাক্য: তুমি বেশি নম্বর পেয়েছ সুতরাং তুমি প্রথম হবে।

জটিল বাক্য: যেহেতু তুমি বেশি নম্বর পেয়েছ সেহেতু তুমি প্রথম হবে।
যৌগিক বাক্য: শিশিরের বয়স যথাসময়ে ষোল হইল, কিন্তু সেটা স্বভাবের ষোলো।
জটিল বাক্য: যদিও শিশিরের বয়স ষোলো তথাপি সেটা স্বভাবের ষোল।
কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাক্য রূপান্তরঃ
সরল বাক্য তার বয়স বাড়লেও বুদ্ধি বাড়েনি।
জটিল বাক্য: যদিও তার বয়স বেড়েছে, তথাপি বুদ্ধি বাড়েনি ৷
যৌগিক বাক্যঃ তার বয়স বেড়েছে কিন্তু বুদ্ধি বাড়েনি।
সরল বাক্য: দরিদ্র হলেও তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ।
জটিল বাক্য: যদিও তিনি অত্যন্ত দরিদ্র, তথাপি তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ।
যৌগিক বাক্য: তিনি অত্যন্ত দরিদ্র, কিন্তু তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ।
সরল বাক্য: দোষ স্বীকার করলে তোমাকে কোনো শাস্তি দেব না।
জটিল বাক্য: যদি দোষ স্বীকার কর, তাহলে তোমাকে কোনো শাস্তি দেব না।
যৌগিক বাক্য: দোষ স্বীকার কর, তবে তোমাকে কোনো শাস্তি দেব না।
সরল বাক্য: কাল সে আসলে আমি যাব।
জটিল বাক্য: যদি সে কাল আসে, তাহলে আমি যাব।
যৌগিক বাক্য: সে কাল আসবে এবং আমি যাব।
সরল বাক্য: মেঘ গর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে।
জটিল বাক্য: যদি মেঘ গর্জন করে, তাহলে ময়ূর নৃত্য করে।
যৌগিক বাক্য; মেঘ গর্জন করে, তবে ময়ূর নৃত্য করে।
সরল বাক্য: মিথ্য কথা বলার জন্য তোমার পাপ হবে।
জটিল বাক্য: যেহেতু তুমি মিথ্যা বলেছ, সেহেতু তোমার পাপ হবে।
যৌগিক বাক্য: তুমি মিথ্যা বলেছ, সুতরাং তোমার পাপ হবে।
সরল বাক্য: সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি।
জটিল বাক্য: যেহেতু আমি সত্য কথা বলিনি, সেহেতু আমি বিপদে পড়েছি।
যৌগিক বাক্য: সত্য কথা বলিনি, তাই বিপদে পড়েছি।
সরল বাক্য: সে পরিশ্রমী হলেও নির্বোধ।
জটিল বাক্য: যদিও সে পরিশ্রমী তথাপি নির্বোধ।
যৌগিক বাক্য: সে পরিশ্রমী বটে, কিন্তু নির্বোধ।
সরল বাক্য: পড়াশুনা করলে জীবনে উন্নতি করতে পারবে।
জটিল বাক্য: যদি পড়াশুনা কর, তাহলে জীবনে উন্নতি করতে পারবে।

যৌগিক বাক্য: পড়াশুনা কর, তবে জীবনে উন্নতি করতে পারবে।
সরল বাক্য: লোভ পরিত্যাগ করলে তুমি সুখে থাকবে।
জটিল বাক্য: যদি লোভ পরিত্যাগ কর, তাহলে সুখে থাকবে।
যৌগিক বাক্য: লোভ পরিত্যাগ কর, তুমি সুখে থাকবে।
অর্থগত ভাবে বাক্যকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:
- বিবৃতিমূলক বাক্য
- প্রশ্নবোধক বাক্য
- অনুজ্ঞাসূচক বাক্য
- আবেগসূচক বাক্য
বিবৃতিমূলক বাক্য
যে বাক্যে কোন বক্তব্য সাধারণভাবে বিবৃত বা বর্ণনা করা হয়, তাকে বিবৃতিমূলক বা বর্ণনাত্মক বাক্য বলা হয়। যেমন-
- সূর্য পূর্বদিকে ওঠে।
- সে রোজ এখানে আসে।
- সে এখন আর আবৃত্তি করে না।
- আজ বৃষ্টি হবে না।
বিবৃতিমূলক বাক্য দুই প্রকার। যথা: হ্যাঁ-সূচক বা অস্তিবাচক বাক্য না-সূচক বা নেতিবাচক বাক্য
হ্যাঁ-সূচক বা অস্তিবাচক বাক্য: যে বাক্যে কোনো ঘটনা, ভাব ও বক্তব্যের অস্তিত্ব বা হ্যাঁ-সূচক অর্থ প্রকাশ পায়, তাকে হ্যাঁ-সূচক বা অস্তিবাচক বাক্য বলে। যেমন:
- সেদিনও মুখ ভার করে ছিল রেনু।
- দিনগুলো বেশ কাটছিল আমাদের।
- আমরা মিছিলে পা বাড়ালাম।
- ওর মা মারা গেছে।
না — সূচক বা নেতিবাচক বাক্য: যে বাক্যে কোন ঘটনায়, কাজে বা ভাবে অস্বীকৃতি, অনস্তিত্ব, নিষেধ বা না-সূচক অর্থ বোঝায়, তাকে না-সূচক বা নেতিবাচক বাক্য বলে। যেমন:
- সেদিনও রেনুর মুখ প্রফুল্ল ছিল না।
- আমাদের দিনগুলো খারাপ কাটছিল না।
- আমরা মিছিলে পা না বাড়িয়ে পারলাম না।
- ওর মা বেঁচে নেই।
প্রশ্নবোধক বাক্য
সংবাদ দান নয়, বরং সংবাদ পাওয়ার জন্য শ্রোতাকে লক্ষ করে যে বাক্য বলা হয়, তার একটি প্রধান রূপ হচ্ছে প্রশ্নবোধক বাক্য। যে বাক্যে কোনো কিছুর জিজ্ঞাসা বা প্রশ্নসূচক অর্থ প্রকাশ করে, তাকে প্রশ্নবোধক বাক্য বলে। যেমন-
তোমার নাম কী?
বাড়ি থেকে আসছ বুঝি?
কোথায় যাচ্ছ?
কেন এসেছ?
যাবে নাকি?
অনুজ্ঞাসূচক বাক্য
যে বাক্যে আদেশ, অনুরোধ, প্রার্থনা, মিনতি ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ পায়, তাকে অনুজ্ঞাসূচক বাক্য বলে। এতে সাধারণত কর্তাটি উহ্য থাকে। যেমন:
- আমার কাজটা করে দিন/ দেবেন। (অনুরোধ)
- প্রভু, দীনের এই প্রার্থনা পূরণ করুন। (প্রার্থনা)
- বাংলাদেশ যেন জয়লাভ করে। (প্রার্থনা)
- ভাল ফলের চেষ্টা কর। (আদেশ) কাছে এস (আদেশ)
- বল বীর, বল উন্নত মম শির। (আদেশসূচক)
- খোদা, তোমার মঙ্গল করুন। (প্রার্থনা)
- লক্ষ্মী বাবা, আমার একটা কথা শোন্ (মিনতি) ধর্ম ও ন্যায়ের পথে চল। (উপদেশ)
আবেগসূচক বাক্য
যে বাক্যে বিস্ময়, হর্ষ, শোক, ঘৃণা, ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি আবেগ প্রকাশ পায়, তাকে আবেগসূচক বাক্য বলে। আবেগসূচক বাক্য মূলত মনের আবেগের প্রকাশ। যেমন-
- কী সাংঘাতিক লোক! (বিস্ময়) ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে,, আমি বনফুল গো! (হর্ষ)
- ছিঃ ছিঃ তোমার এই কাজ! (ঘৃণা) তুমি এত নীচ! (ঘৃণা)
- হায় হায়! কী যন্ত্রণায় যে পড়েছি। (শোক) এত বড় স্পর্ধা! মুখের ওপর কথা বলে। (ক্রোধ)
- ওরে বাবা রে, খেয়ে ফেলল রে! (ভয়)
অর্থগত বাক্যের রূপান্তর
- অস্তিবাচক থেকে নেতিবাচকঃ
অস্তিবাচকঃ আরও কথা আছে।
নেতিবাচকঃ কথা শেষ হয় নি।
অস্তিবাচকঃ জামিল বাড়িতে আছে।
নেতিবাচকঃ জামিল বাড়িতে অনুপস্থিত নয়।
অস্তিবাচকঃ আজ চাঁদ উঠেছে।
নেতিবাচকঃ আজ চাঁদ না উঠে পারে নি।
অস্তিবাচকঃ তোমার সব জিনিসই দামী।
নেতিবাচকঃ তোমার কোনো জিনিসই সস্তা নয়।
অস্তিবাচকঃ প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে।
নেতিবাচকঃ প্রিয়ংবদা অযথার্থ কহে নাই।

অস্তিবাচকঃ মিথ্যাবাদীকে সবাই অপছন্দ করে।
নেতিবাচকঃ মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না।
অস্তিবাচকঃ তবু না বলা কথাটি সবাই মেনে নেয়।
নেতিবাচকঃ তবু না বলা কথাটি সবাই মেনে না নিয়ে পারে না।
- নেতিবাচক থেকে অস্তিবাচক
নেতিবাচকঃ তার আদর্শ বিস্মরণযোগ্য নয়।
অস্তিবাচকঃ তার আদর্শ স্মরণযোগ্য।
নেতিবাচকঃ পুকুরপাড়ে এখন কেউ নেই।
অস্তিবাচকঃ পুকুরপাড়ে এখন সবাই অনুপস্থিত।
নেতিবাচকঃ তাকে নির্দয় মনে হয় না।
অস্তিবাচকঃ তাকে সদয় মনে হয়।
নেতিবাচকঃ ভালবাসার দানে কোনো অপমান নেই।
অস্তিবাচকঃ ভালবাসার দানে অনেক সম্মান আছে।
নেতিবাচকঃ শহীদের মৃত্যু নেই।
অস্তিবাচকঃ শহীদেরা অমর।
নেতিবাচকঃ তাদের ভুলটা ভাঙতে দেরি হয় না।
অস্তিবাচকঃ অচিরেই তাদের ভুল ভাঙে।
- অস্তিবাচক থেকে প্রশ্নবোধক
সবাই অধীনতার বন্ধন ছিন্ন করতে চায়।
কে না অধীনতার বন্ধন ছিন্ন করতে চায়?
বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের জনক।
বিদ্যাসাগর কি বাংলা গদ্যের জনক নয়?
জীবনানন্দ দাশ বাংলাদেশে জন্মেছেন।
জীবনানন্দ দাশ কী বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেন নি?
ভুল সকলেই করে
ভুল কে না করে?
- প্ৰশ্ববোধক থেকে নেতিবাচক
প্ৰশ্ববোধকঃ কোথাও কি তিনি আছেন?
নেতিবাচকঃ কোথাও কি তিনি নেই?
- অস্তিবাচক থেকে বিস্ময়সূচক
অস্তিবাচকঃ গোলাপটি অত্যন্ত সুন্দর।
বিস্ময়সূচকঃ বাহ! কী সুন্দর গোলাপটি।
বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় অর্থাৎ বাক্য নিয়ে আজকে এই পর্যন্তই। আশা করি এই আর্টিকেলটি যেকোনো চাকরি পরীক্ষায় প্রস্তুতির ক্ষেত্রে আপনাকে কিছুটা হলেও সাহায্য করবে।

FAQs
যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি বক্তার কোন মনোভাবকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে তাকে বাক্য বলে।
বাক্যের অর্থ পরিবর্তন না করে বাক্যের প্রকাশভঙ্গি বা গঠনরীতিতে পরিবর্তন করাকেই বাক্য রূপান্তর বলা হয়।
বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে শব্দ ।